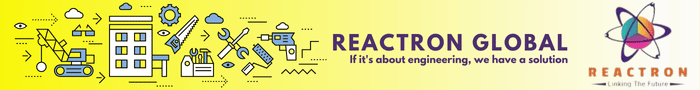বেশ কিছুদিন আগে কৃষি বিষয়ক একটা সভায় কৃষি বিপণনের একজন গণ্যমান্য ব্যাক্তি বর্তমান অবস্থার কথা তুলে ধরতে কিছু কথা বলেন, যার সারমর্ম কিছুটা এমনঃ
“উপমহাদেশে গ্রামবাংলার অধিবাসীদের মধ্যে বিশেষ করে মহিলারা বিশেষ ধরণের ক্ষমতাধারী হয়ে থাকেন। ইংরেজীতে অনেকেই একে বলেন – ‘ইনট্যুশান’ । তারা বীজ স্পর্শ করেই বলে দিতে পারেন কোন বীজ থেকে উন্নত মানের ফসল হবে আর কোন বীজ বন্ধ্যা। কালক্রমে এই ক্ষমতা বিলীন হয়ে যাচ্ছে যার কারণ হয়ত কৃষিতে অত্যাধিক মেশিনের ব্যবহার আর মানবিক স্পর্শের অভাব।”
স্বীকার করতেই হবে, এই ক্রমবর্ধনশীল জনসংখ্যার দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা আনার জন্য মেশিনের ব্যাবহার অপরিহার্য। তবে কথাগুলো আমাকে যা ভাবাল সেটা হচ্ছে যন্ত্রের ব্যবহারের সাথে সাথে হয়তোবা আমরা শিকড়ের সাথে সম্পর্ক হারাতে শুরু করছি। এমন কি হতে পারে, আমাদের চারপাশে স্বতন্ত্রের যে হাহাকার তার সাথে এই শেকড়ের সাথে বিচ্ছিন্নতার কোন যোগসাজশ আছে?
মসলিন আর জামদানি নিয়ে লিখতে বসে কৃষি, মাটি এসব নিয়ে কেন বলছি? একটু ব্যাখ্যা করি কেন জামদানির সাথে আমাদের সম্পর্কটা শেকড়ের।
জামদানি উপমহাদেশে প্রথম কবে আসে সেটা সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তবে উপমহাদেশের ২০০০ বছরের পুরানো ঐতিহ্যবাহী বুনন কৌশল মসলিনের ৩৬ রকম প্রকারের একটি হল জামদানি। এখন থেকে প্রায় ১৬০ বছর আগে “ফুটি কাপাশ” নামক তুলা প্রজাতির শেষ গাছটি বিলীন হয়ে যায়। এই গাছ থেকেই তৈরী হত বিশ্ববিখ্যাত মসলিন। ১৭৯০-১৭৯১ সালে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় এই মসলিন চাষের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয় (গজনবী ২০০৬: ৮৪-৮৫)। এমনকি চট্টগ্রামেও এমন তুলা চাষের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বক্ষ্মপুত্র আর মেঘনা নদীর তীর ঘেষে, মূলত বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রজাতীর কাপাস বা তুলা গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মাত, যেটা বাংলাদেশে চাষ হওয়া সবচেয়ে পুরানো ফসলগুলোর একটি। রক্সবার্গের মতে “কাপাশ”, বা সংস্কৃত ভাষায় “কার্পাস” এর অনেক রকম প্রজাতি ঢাকায় পাওয়া যেত, যা থেকে সূক্ষ্মতম আর উন্নতমানের তুলা প্রস্তুত করা হত (রক্সবার্গ ১৮৩২: ১৮৪)। শুধুমাত্র বাংলাদেশের এই বিশেষ এলাকার তাপমাত্রা আর আর্দ্রতায় নারায়নগঞ্জ, সোনারগাঁও, ফিরিঙ্গি-বাজার, বিক্রমপুর, রাজেন্দ্রপুর, শীতলক্ষ্যা নদীর পাড় ঘেষে বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর পরিমাণে তুলা চাষের নিশানা পাওয়া যায়। এই কাপাশ তুলা থেকেই রাজধানীর নিকটবর্তী “কাপাশিয়া” এলাকার নামকরণ হয়।

কাল-ক্রমানুসারে মসলিনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
মসলিনের সবচেয়ে পুরানো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায় মৌর্য সাম্রাজ্যের (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২১-২৯৭ শতক) নানান রকম টেরাকোটা আর খোদাই থেকে। রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সভার বর্ণনায় তৎকালীন ভারতীয়দের বিবরণ পাওয়া যায়ঃ “তাদের পরণে থাকত কারুকার্যখচিত সূক্ষ্ণ মসলিন আর হাত ও কানে থাকত স্বর্নখচিত বালা ও দুল”।


তবে তারও আগে রোম, মিশর, ইথিওপিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে মসলিন রপ্তানী হত। কথিত আছে যে মিশরীয় মমিদের অতি দূর্লভ আর দামী মসলিন দিয়ে মোড়ানো হত। উইলফ্রেড এইচ শফ এর “Periplus of the Erythraean Sea” বইয়ে বলা আছে প্রথম দশকের মাঝামাঝি সময়ে লোহিত সাগর দিয়ে ভারত আর অন্যান্য দেশের মধ্যে মসলিনের সাথে হাতির দাঁত, কচ্ছপের খোল, গন্ডারের শিং প্রভৃতি দুর্লভ সামগ্রী বিনিময় হত। এতে মোটা ধরনের মসলিনকে মলোচিনা, প্রশস্ত ও মসৃণ মসলিনকে মোনাচি এবং সর্বোৎকৃষ্ট মসলিনকে গেনজেটিক বা গঙ্গাজলী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
তবে মসলিনের নামডাক তার স্বর্ণশিখরে পৌঁছায় মুঘল আমলে। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলায় মরক্কো থেকে আগত পর্যটক ইবনে বতুতা তার “কিতাবুর রেহালা” বইয়ে সোনারগাঁওয়ে তৈরি সুতি বস্ত্রের বিশেষ প্রশংসা করেন। সেই সময়ের সুফী কবি আমীর খসরু তার “নিয়ায়াতুল কামাল” বইয়ে ঢাকার মসলিনের বর্ণনা করে বলেনঃ
“এর ৬ গজ কাপড় একটা তর্জনীর আংটির মধ্যে দিয়ে পার হয়ে যায় অথচ তীক্ষ্ণ সুচ এর ভেতরে সহজে প্রবেশ করানো যায় না। এটা এতই সূক্ষ্ম আর হাল্কা যেন পড়লে মনে হয় শুধুমাত্র পরিচ্ছন্ন পানির ধারা ব্যতীত আর কিছু পরিহিত নেই।”
পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে আসা চীনা লেখকরাও এখানকার সুতি বস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মুঘল সম্রাট আকবরের সভাসদ আবুল ফজল সোনারগাঁওয়ে প্রস্তুতকৃত এই সূক্ষ্ণ সুতি বস্ত্রের প্রশংসা করেন। সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে ঢাকাকে বাংলার রাজধানী ঘোষণার পর হতেই ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা বাংলায় আসা শুরু করেন। এসকল বণিক কোম্পানিগুলোর তৎকালীন দলিল-দস্তাবেজ এবং সমকালীন ইউরোপীয় লেখকদের বিবরণে মসলিন সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। (জেমস টেইলরের রচনা অবলম্বনে ইতিহাসবিদ আব্দুল করিমের গ্রন্থ থেকে সংগৃহিত উপাত্ত)। বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের রাণী মারি অঁতোয়ানেত আর নেপোলিয়ানের প্রথম স্ত্রী জোসেফিন মসলিনকে ফ্রান্সে জনপ্রিয় করে তোলে। এমনকি বিশ্বখ্যাত ডিজনীর গল্পেও উঠে এসেছে মসলিনের কথা – রেভারেণ্ড অ্যালেকজান্ডার হুইটেকারের ভাষ্যে এসেছে বিখ্যাত চরিত্র পোকাহন্তাসের পরনে ছিল ঢাকার তাতে বোনা শুভ্র মসলিন।

মসলিনের পতন ঘটে পলাশির যুদ্ধের পরে উনবিংশ শতাব্দীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন আমলে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমলে স্থানীয় বস্ত্রের উপর ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ কর স্থাপন করা হয় আর আমদানীকৃত পন্যে কর ছিল ১ থেকে ২ শতাংশ। শিল্প বিপ্লবের সাথে সাথে কলে তৈরী জামায় নীলের ব্যবহার শুরু হয়। এই নীল চাষে বাধ্য করার কারণে বাংলার উর্বর অঞ্চলগুলোতে তুলার বদলে চাষ হতে থাকে নীল আর এভাবেই একসময়ে শেষ কাপাশ গাছ আর তাঁতিদের অর্থনৈতিক দুর্দশার মাধ্যমে উপমহাদেশে মসলিনের হাজার বছরের ঐতিহ্য বিলীন হয়ে যায়।
মসলিনের প্রকারভেদ
মসলিনের বিভিন্ন প্রকারভেদ তৈরি হয়েছে সূক্ষ্মতা, বুনন আর নকশার পার্থক্যের কারণে। মুনতাসীর মামুনের “ঢাকার মসলিন” (ফেব্রুয়ারি ২০০৫ সংস্করণ) থেকে বিভিন্ন রকম মসলিনের বর্ণনা পাওয়া যায়।
১। মলবুস খাসঃ আঠারো শতকের শেষদিকে মলবুস খাসের মতো আরেক প্রকারের উঁচুমানের মসলিন তৈরি হত, যার নাম ‘মলমল খাস’। এগুলো লম্বায় ১০ গজ, প্রস্থে ১ গজ, আর ওজন হত ৬-৭ তোলা। ছোট্ট একটা আংটির মধ্যে দিয়ে এ কাপড় নাড়াচাড়া করা যেত। এগুলো সাধারণত রপ্তানি করা হত।
২। সরকার-ই-আলাঃ এ মসলিনও মলবুস খাসের মতোই উঁচুমানের ছিল। বাংলার নবাব বা সুবাদারদের জন্য তৈরি হত এই মসলিন। সরকার-ই-আলা নামের জায়গা থেকে পাওয়া খাজনা দিয়ে এর দাম শোধ করা হত বলে এর এরকম নামকরণ। লম্বায় হত ১০ গজ, চওড়ায় ১ গজ আর ওজন হত প্রায় ১০ তোলা।
৩। ঝুনাঃ ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ জেমস টেইলরের মতে ‘ঝুনা’ শব্দটি এসেছে হিন্দি ‘ঝিনা’ থেকে, যার অর্থ হল সূক্ষ্ণ। ঝুনা মসলিনও সূক্ষ্ম সুতা দিয়ে তৈরি হ্ত, তবে সুতার পরিমাণ থাকত কম । তাই এ জাতীয় মসলিন হালকা জালের মতো হত দেখতে। একেক টুকরা ঝুনা মসলিন লম্বায় ২০ গজ, প্রস্থে ১ গজ হত। আর ওজন হত মাত্র ২০ তোলা। এই মসলিন বিদেশে রপ্তানি করা হত না, পাঠানো হতো মুঘল রাজ দরবারে। সেখানে দরবারের বা হারেমের মহিলারা গরমকালে এ মসলিনের তৈরি জামা গায়ে দিতেন।
৪। নয়নসুখঃ মসলিনের একমাত্র এই নামটিই বাংলায়। সাধারণত গলাবন্ধ রুমাল হিসেবে এর ব্যবহার হত। এ জাতীয় মসলিনও ২০ গজ লম্বা আর ১ গজ চওড়া হত।
৫। আব-ই-রওয়ানঃ ‘আব-ই-রওয়ান’ ফার্সি শব্দ, যার অর্থ প্রবাহিত পানি। এই মসলিনের সূক্ষ্মতা বোঝাতে প্রবাহিত পানির মতো টলটলে উপমা থেকে এর নামই ‘আব-রওয়ান’ হয়ে যায়। লম্বায় হত ২০ গজ, চওড়ায় ১ গজ, আর ওজন হত ২০ তোলা। আব-ই-রওয়ান সম্পর্কে প্রচলিত গল্পগুলোর সত্যতা নিরূপণ করা না গেলেও উদাহরণ হিসেবে বেশ চমৎকার। যেমনঃ একবার সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারে তাঁর মেয়ে উপস্থিত হলে তিনি মেয়ের প্রতি রাগান্বিত হয়ে বললেন তোমার কি কাপড়ের অভাব নাকি? তখন মেয়ে আশ্চর্য হয়ে জানায় সে আব-ই-রওয়ানের তৈরী সাতটি জামা গায়ে দিয়ে আছে। অন্য আরেকটি গল্পে জানা যায়, নবাব আলীবর্দী খান বাংলার সুবেদার থাকাকালীন তাঁর জন্য তৈরী এক টুকরো আব-ই-রওয়ান ঘাসের উপর শুকোতে দিলে একটি গরু এতটা পাতলা কাপড় ভেদ করে ঘাস আর কাপড়ের পার্থক্য করতে না পেরে কাপড়টা খেয়ে ফেলে। এর খেসারতস্বরূপ আলীবর্দী খান ওই চাষীকে ঢাকা থেকে বের করে দেন।
৬। খাসসাঃ ফার্সি শব্দ ‘খাসসা’ নামক এই মসলিন ছিল মিহি আর সূক্ষ্ম, অবশ্য বুনন ছিল ঘন। সপ্তদশ শতাব্দীতে সোনারগাঁ বিখ্যাত ছিল খাসসার জন্য। আবার অষ্টদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে জঙ্গলবাড়ি বিখ্যাত ছিল এ মসলিনের জন্য। তখন একে ‘জঙ্গল খাসসা’ বলা হত। অবশ্য ইংরেজরা একে ডাকত ‘কুষা’ বলে।
৭। শবনমঃ ‘শবনম’ কথাটার অর্থ হলো ভোরের শিশির। ভোরে শবনম মসলিন শিশিরভেজা ঘাসে শুকোতে দেয়া হলে শবনম দেখাই যেত না, এতটাই মিহি আর সূক্ষ্ম ছিল এই মসলিন। ২০ গজ লম্বা আর ১ গজ প্রস্থের শবনমের ওজন হত ২০ থেকে ২২ তোলা।
৮। বদন সুখঃ এ জাতীয় মসলিনের নাম থেকে ধারণা করা হয় সম্ভবত শুধু জামা তৈরিতে এ মসলিন ব্যবহৃত হত। কারণ ‘বদন’ মানে শরীর। এর বুনন ঘন হত না। এগুলো ২৪ গজ লম্বা আর দেড় গজ চওড়া হত, ওজন হত ৩০ তোলা।
৯। সর-বন্ধঃ ফার্সি শব্দ ‘সর-বন্ধ’ মানে হল মাথা বাঁধা। প্রাচীন বাংলা উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা মাথায় পাগড়ি বাঁধতেন, যাতে ব্যবহৃত হত এই জাতের মসলিন। লম্বায় ২০ থেকে ২৪ গজ আর চওড়ায় আধা থেকে এক গজ হত; ওজন হত ৩০ তোলা।
১০। ডোরিয়াঃ ডোরা কাটা মসলিন ‘ডোরিয়া’ বলে পরিচিত ছিল। লম্বায় ১০ থেকে ১২ গজ আর চওড়ায় ১ গজ হত। শিশুদের জামা তৈরি করে দেয়া হত ডোরিয়া দিয়ে।
মসলিন থেকে জামদানি
জামদানি কার্পাস তুলা দিয়ে প্রস্তুত একধরনের পরিধেয় বস্ত্র। প্রাচীনকালের মিহি মসলিন কাপড়ের উত্তরাধিকারী হিসেবে জামদানি শাড়ি বাঙ্গালি নারীদের অতি পরিচিত। মসলিনের উপর নকশা করে জামদানি কাপড় তৈরি করা হয়। জামদানি বলতে সাধারণত শাড়িকেই বোঝান হয়। তবে জামদানি দিয়ে নকশি ওড়না, কুর্তা, পাগড়ি, রুমাল, পর্দা প্রভৃতিও তৈরি করা হত। সপ্তদশ শতাব্দীতে জামদানি দিয়ে নকশাওয়ালা শেরওয়ানির প্রচলন ছিল। এ ছাড়া, মুঘল আমলের শেষের দিকে নেপালে ব্যবহৃত আঞ্চলিক পোশাক রাঙ্গার জন্যও জামদানি কাপড় ব্যবহৃত হত। তবে আগেকার যুগে ‘জামদানী’ বলতে বোঝানো হতো নকশা-করা মসলিনকে। ধারণা করা হয় জামদানি শব্দটা এসেছে ফার্সি শব্দ ‘জামা-ই’ যার অর্থ ‘কাপড়’ থেকে। আবার ফার্সিতে ‘জমাদান’ অর্থ আলমারি।
বুনন শিল্প
জামদানির বুনন নকশাই একে অনন্য করে তুলেছে। আগে শুধুমাত্র সাদা আর হালকা ধূসর বাদামী রংয়ে জামদানি বোনা হত। শাড়ি সহ ব্যবহার্য নানা পোশাক হিসেবে জামদানির ব্যাবহার ছিল। জামদানি একটি শাড়ি বুনতে একই সাথে দুইজন তাতীকে কাজ করতে হয়। সাধারণত একজন মাস্টার তাঁতি আর তার শিক্ষানবিস একসাথে একটা জামদানি বোনার কাজ করে থাকে। বিভিন্ন সুতার কাউন্টের সাথে সাথে জামদানির উৎকর্ষের মাত্রা নির্ধারিত হয়। বর্তমানে ঢাকার জামদানিতে ৩৫ থেকে ২০০ কাউন্ট পর্যন্ত সুতার ব্যবহার হয়ে থাকে আর বিভিন্ন রংয়ের জামদানি প্রস্তুত করা হয়। আর একেকটা শাড়ী তৈরি করতে ২ সপ্তাহ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।
বিস্ময়কর ব্যপার হল, জামদানির নকশার কোন প্রকার ছাঁচ তৈরি করা হয় না। তাঁতি তার মনের মাধুরী মিশিয়ে এই জটিল সুতার বুনন তার মাথার ভেতরে ঠিক করে ফেলেন। তাদের এই বিস্ময়কর ক্ষমতার সাথে গণিতবিদের তুলনা করেছেন অনেক বিশেষজ্ঞ আর ইতিহাসবিদ। বুননের কিছু সাধারণ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমনঃ আঙ্গুর, বাঘের পা, গোলাপ, কলমিলতা, কাকড়া, কচু, কলা, শঙ্খ, সাপ ইত্যাদি।

জামদানি ও বর্তমান
UNESCO ২০১৩ সালে জামদানিকে ‘Intangible Cultural Heritage of Humanity’ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। কোন অঞ্চলের সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের অবিভেদ্য শিল্প বা কৌশলকে এমন উপাধি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। যেমনঃ জ্যামাইকার রেগে সঙ্গীত, স্পেনের ফ্ল্যামেংকো, ইন্দোনেশিয়ার বাটিক, চীনের এবাকাস, ইন্ডিয়ার ইয়োগা ইত্যাদি। তবে বর্তমানে পৃষ্ঠপোশকতার অভাবে জামদানি তাঁতিদের দৈন্য দশা চলছে। বর্তমানে বাংলাদেশ এবং কলকাতায় জামদানি নিয়ে কাজ করার চেষ্টা চলছে। তার পাশাপাশি কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগও গ্রহণ করা হচ্ছে; যা এই হারানো ঐতিহ্যবাহী বুননশিল্প পুনরুদ্ধারের জন্য হয়ত যথেষ্ট নয়।
বর্তমানে নারায়নগঞ্জের রূপগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদীর ধারে তাঁতিদের বসবাস রয়েছে। প্রায় ১৫০০ তাঁতি নিয়ে এই অঞ্চলে প্রস্তুত হয় বিভিন্ন রকম জামদানি শাড়ি। আর্থিক অনটনের কারণেই তাদের অনেকে পেশা পরিবর্তন করে বেছে নিচ্ছেন অন্যান্য পেশা।
সবশেষে বলতে চাই, বিশ্বজোড়া এই অগ্রগতির স্রোতে আমরা হয়ত নিজেরা অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছি। হয়ে উঠছি আরো অনেক কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন আর কর্মক্ষম। তবে সবকিছুরই একটা বিনিময় মূল্য রয়েছে। লেখার শুরুতে যা বলেছিলাম, উৎপাদন বাড়াতে কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার হয়ত স্পর্শ করে বীজের উর্বরতা বোঝার ক্ষমতা মানুষের থেকে নিয়ে যাচ্ছে। হয়ত শিক্ষানবিস তাঁতি অর্থাভাবে অটোরিকশা চালাচ্ছে আর হারিয়ে ফেলছে এই জটিল বুনন অনায়াসে তৈরি করার ক্ষমতা। আমরাও হয়ত দিন দিন শেকড় থেকে অনেক দূরে চলে যেয়ে হারাচ্ছি নিজস্বতা।
নাজিফা তাবাসসুম পিউলি একজন স্থপতি, জামদানি গবেষক, উদ্যোক্তা, এবং সঙ্গীতজ্ঞ